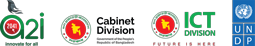-
উপজেলা সম্পর্কিত
ইতিহাস-ঐতিহ্য
ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক
-
উপজেলা পরিষদ
আর্থিক ব্যবস্থাপনা
স্থায়ী কমিটি
-
আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কমিটি
-
যোগাযোগ এবং ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন
-
কৃষি ও সেচ
-
মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা
-
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা
-
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
-
যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন
-
নারী ও শিশু উন্নয়ন
-
সমাজ সেবা
-
মুক্তিযোদ্ধা
-
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ
-
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
-
সংস্কৃতি
-
বন ও পরিবেশ
-
বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং এবং নিয়ন্ত্রণ
-
অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ
-
জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ
-
আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কমিটি
-
উপজেলা প্রশাসন
সংগঠন সম্পর্কিত
কর্মসূচি ও সভা
-
সরকারি অফিস
আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ক
শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক
কৃষি, মৎস্য, প্রাণি ও খাদ্য বিষয়ক
স্বাস্থ্যও পরিবেশ বিষয়ক
প্রকৌশল এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক
ভূমি ও রাজস্ব বিষয়ক
-
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
-
ই-সেবা
জাতীয় ই-সেবা
মোবাইল অ্যাপ
উপজেলা আইসিটি কেন্দ্র (UICTC)
ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রসমূহ
- গ্যালারি
- জাতীয় সংগীত
-
উপজেলা সম্পর্কিত
ইতিহাস-ঐতিহ্য
ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক
-
উপজেলা পরিষদ
আর্থিক ব্যবস্থাপনা
সম্পদ বিবরণী
স্থায়ী কমিটি
- আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কমিটি
- যোগাযোগ এবং ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন
- কৃষি ও সেচ
- মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
- যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন
- নারী ও শিশু উন্নয়ন
- সমাজ সেবা
- মুক্তিযোদ্ধা
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
- সংস্কৃতি
- বন ও পরিবেশ
- বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং এবং নিয়ন্ত্রণ
- অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ
- জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ
প্রকল্প সমূহ
-
উপজেলা প্রশাসন
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
সংগঠন সম্পর্কিত
কর্মসূচি ও সভা
-
সরকারি অফিস
আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ক
শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক
কৃষি, মৎস্য, প্রাণি ও খাদ্য বিষয়ক
স্বাস্থ্যও পরিবেশ বিষয়ক
প্রকৌশল এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক
ভূমি ও রাজস্ব বিষয়ক
-
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
-
ই-সেবা
জাতীয় ই-সেবা
মোবাইল অ্যাপ
উপজেলা আইসিটি কেন্দ্র (UICTC)
ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রসমূহ
-
গ্যালারি
ফটোগ্যালারি
ভিডিও গ্যালারি
-
জাতীয় সংগীত
জাতীয় সংগীত (অডিও)
জাতীয় সংগীত (মিউজিক ট্র্যাক)
জাতীয় সংগীত (পাঠ)

এই পদ্মা, এই মেঘনা, এই যমুনা, সুরমা নদী তটে
দেশের অন্যতম বৃহত্তম একটি নদী যার নাম পদ্মা।প্রাকৃতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ প্রধানতঃ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর বাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপ। হিমালয় থেকে উদ্ভুত নদীগুলোর গতিপথ বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। যার ফলে এই নদীগুলোর তীরে যেমনি গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ নানা শহর, তেমনি তারা আবার নদীগর্ভে বিলিনও হয়ে যায়। তাই বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের অতীত চিহ্ন খুব কম পাওয়া যায়। যেমন আজ আমরা গঙ্গার যে গতিপথ দেখতে পাই তা ষোড়শ শতাব্দিতেও ভিন্ন ছিল। সে সময় তা আরও উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এসে গৌড় শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত। বর্তমান ফারাক্কা বাধ নির্মাণের পূর্বে গঙ্গার পানি মূলতঃ পদ্মা দিয়েই প্রবাহিত হতো, কিন্তু আগে ভাগীরথীই ছিল গঙ্গার প্রবাহ পথ। সেও শ’পাচেক বৎসর আগের কথা।
লালমাই পাহাড়ের লাল মাটি, সম্ভবতঃ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীমালার বহু পূর্বের কোন নদীমালার ব্যবস্থার দ্বারা গঠিত হয়েছিল। চান্দিনা সমভূমি পরবর্তি কোন সময়ের নতুন পলীর দ্বারা গঠিত। আর পশ্চিমে এখন যে মেঘনা প্লাবিত সমভূমি দেখা যায়, সেটাই সর্বশেষ পলি গঠিত ভূমি। গোমতি নদী যুগে যুগে বহুবার তার গতি পরিবর্তন করেছে। বাংলাদেশে বৌদ্ধ যুগে (৬৫০ থেকে ১০০০ খৃঃ পর্যন্ত্য) যে সকল ন গরের পত্তন হয়েছিল যেমন বরকামতা, দেব-পর্বত, রহিতগিরি সেই সময়ে প্রবাহিত কোন কোন নদীর পাশে অবস্থিত ছিল। নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হওয়ায় এগিলো পরিত্যক্ত হয় বলে ধারণা করা হয়। সমতটের রাজধানী কর্মান্ত বা বড়কামতা এক সময় খেরু নদীর তীরে অবস্থিত ছিল, যা গোমতিরই কোন অতীত ধারা ছিল বলে মনে করা হয়।
ধীরভূমি উৎক্ষেপের ফলে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, পুরাতন মেঘনা ও পুরাতন তিস্তা নদী এক সময় তাদের গতিপথ পরিবর্তন করে, কিন্তু তার আগেই তারা যে পলি রেখে গিয়েছিল তাই বর্তমান ব্রাহ্মনবাড়িয়া, চান্দিনা ও নোয়াখালির সমভূমিতে দেখা যায়। বর্তমানে নদীর যে গতিগুলো দেখা যাচ্ছে তা মোটামুটিভাবে বিগত ২০০ বছর ধরে আছে। প্রাচীনকালে পশ্চিমবঙ্গের তমুলকে একটি বিখ্যাত নদীবন্দর ছিলযা সরস্বতি নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে পরিত্যক্ত হয়। গত চারশ বছরে পদ্মার গতিও যথেস্ট পরিবর্তিত হয়েছে। ধারণা করা হয় তা রামপুর বোয়ালিয়ার পাশ দিয়ে, চলন বিলের মধ্য দিয়ে ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার মধ্য দিয়ে ঢাকা নগরী অতিক্রম করে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে।
এমনকি অস্টাদশ শতাব্দিতেও পদ্মার নিম্ন অববাহিকা ছিল বর্তমান গতিপথের অনেক দক্ষিণে। পদ্মা সেকালে ফরিদপুর ও বাকেরগন্জ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বর্তমান চাঁদপুরের প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে শাহবাজপুর দ্বীপের উত্তরে মেঘনায় মিলেছিল। একসময়কার বিখ্যাত নগরী রাজনগর ছিল তার বাম তীরে এবং এর সন্নিকটে কালিগঙ্গা নদী মেঘনা ও পদ্মার মধ্যে সংযোগ সাধন করত।
বর্তমানে ব্রহ্মপুত্র নদী যমুনা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। কিন্টু আগে ব্রহ্মপুত্রের গতি গারো পর্বতমালার পশ্চিম দিক দিয়ে পূর্ব দক্সিণে প্রবাহিত হয়ে জামালপুর, ময়মনসিংহ ও মধুপুর জঙ্গলের পাশ দিয়ে ও ঢাকা জেলার পূর্বাঞ্চল হয়ে নাঙ্গলবন্দ ও সোনারগাঁও পাশে রেখে শেষে নারায়নগন্জের ধলেশ্বরীর সাথে মিলিত হতো। করতোয়া এককালে একটি বিশাল ও হিন্দুদের পবিত্র নদী ছিল। এর পাশে ছিল মৌর্যদের বিখ্যাত পুন্ড্রবর্ধন নগর। জানা যায় যে ১৭৮৭ সালে তিস্তায় বিশাল বন্যা হয় এবং তার ফলে সে নতুন গতিপথ পায়।
চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের মাতামুহুরী নদীটি প্রায় প্রত্যেক বন্যাতেই গতি পরিবর্তন করেছে। হাজার হাজার বছর ধরে বাংলাদেশের উদ্বেল নদীগুলোর এই ভাঙাগড়া চলছে। এই দেশের অর্থনীতিতে নদীর প্রভাব ছিল অসামান্য। যখনই কোন বড় বন্যা হয়েছে তখনই নদীর গতি পরিবর্তনে ধ্বংস হয়েছে বহু নগর-বন্দর-জনপদ। কোশী নদীর গতি পরিবর্তনে সৃষ্ট জলাভূমিতেই গৌড় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। একইভাবে গোপালগন্জের নিকটস্থ বিখ্যাত বন্দর ও সভ্যতার কেন্দ্র কোটালিপদ নগরীও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এরূপ অনুমান করা হয় যে, বর্তমান সুন্দরবনের অভ্যন্তরে এক সময় সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মগ-পর্তুগীজ দস্যুদের অত্যাচারে তা ধ্বংস হয়।
বাংলাদেশের জীবনে এই নদীগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। যেকোন বিদেশী পর্যটক-পরিব্রাজকই এই প্রমত্তা নদীগুলোর বর্ননা দিয়েছেন। নদীপথ ব্যবহার করে তারা ভ্রমণ করেছেন বাংলা। এর দুই তীরে দেখছেন অসংখ্য বৃক্ষরাজী আর সুদৃশ্য চিত্রা হরিণের দল। এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও নদীপথই ছিল বহুল ব্যবহৃত ও সর্বাধিক জনপ্রিয়। নদী একদিকে যেমন অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে, আবার তার ভয়াবহ বন্যার রূপ জনজীবনে নিয়ে এসেছে বিপর্যয়, নদী ভাঙনে গৃহহীন হয়েছে শত শত মানুষ। সব মিলিয়ে আমাদের জীবনে এই নদীগুলোর রয়েছে আবেগময় অবস্থান। তাই এই নদীগুলো নিয়ে রচিত হয়েছে শত শত গান। যেমন নগরাঞ্চলে তেমনি পল্লী জনপদে।
‘ও নদীরে, একটি কথা শুধাই শধু তোমারে,
বল কোথায় তোমার দেশ, তোমার চলার নাইকো শেষ?
ও নদীরে ……।’
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস